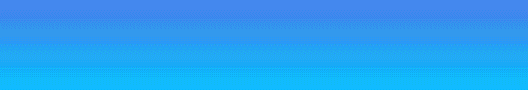ড. ফারজানা ইসলাম
বঙ্গবন্ধু, বাঙালি ও বাংলাদেশ যেমন একই সূত্রে গ্রথিত, তেমনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবও (যিনি বঙ্গবন্ধুর প্রিয় রেণু) পরস্পর অবিচ্ছেদ্য নাম। ফজিলাতুন্নেছার শৈশবের সঙ্গী শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁরা একই পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন। জীবন চলার পথে একে অপরের অপরিহার্যতার প্রমাণ দিয়েছেন ১৫ আগস্টের কালরাত্রিতে। এই মহীয়সী নারী জন্মেছিলেন আগস্ট মাসেরই ৮ তারিখে।
নবীন প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ আলোচনায় বঙ্গমাতার জীবনাচারও অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উদ্ভাসিত। খোকা থেকে মুজিব, মুজিব থেকে মুজিব ভাই, মুজিব ভাই থেকে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু থেকে জাতির পিতা হয়ে ওঠার পেছনে যার অবদান অনস্বীকার্য, তিনি হচ্ছেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব।
বঙ্গমাতার পিতা শেখ মোহাম্মদ জহুরুল হক যশোরে কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টে অডিটর পদে চাকরি করতেন। প্রথম কন্যা বেগম জিনাতুন্নেছা, ডাকনাম জিন্নি ৫ বছর এবং কনিষ্ঠ কন্যা ২ বছর বয়সী ফজিলাতুন্নেছা, ডাকনাম রেণুকে রেখে পিতা শেখ মোহাম্মদ জহুরুল হক এবং পরে মাতা হোসনে আরা বেগম মৃত্যুবরণ করেন। তখন এই দুই নাবালিকা অনাথ মেয়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব এসে বর্তায় ৮০ বছরের বৃদ্ধ দাদা শেখ মো. আবুল কাসেমের ওপর। পিতৃমাতৃহারা হয়ে শিশু ফজিলাতুন্নেছা বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফুর রহমান আর মাতা সায়েরা খাতুনের আদরে বঙ্গবন্ধুর অন্যান্য ভাইবোনের সঙ্গে খেলার সাথী হয়ে বড় হয়েছেন। তিনি মাত্র ১৩ বছর বয়সে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন শেখ মুজিবের সঙ্গে। বঙ্গবন্ধুর ভাষায় ‘বিয়ে কী তা তো বুঝলাম না। শুনলাম, রেণুর দাদা আমার আব্বাকে এক রকম হুকুম জারি করেছিলেন। মুরব্বিরা তাঁর কথা অবহেলা করার অবকাশ পাননি। সুতরাং বিয়ে রেজিস্ট্রি করা হয়ে গেল।’ ফজিলাতুন্নেছা বঙ্গবন্ধুর স্কুল জীবনের সাথী হলেও প্রকৃত জীবন সাথী হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর এন্ট্রান্স পাস করার পর। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, তাঁদের বিয়ের ফুলশয্যা হয়েছিল ১৯৪২ সালে। বঙ্গবন্ধুর স্কুল জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁর পিতার সান্নিধ্যে কেটেছে। বঙ্গবন্ধু ১৯৪২ সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ঘটে।
দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গেই তার রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রামে বঙ্গমাতা নিজেকে যুক্ত করেছেন। তিনি ছাত্রলীগকে সব ধরনের সহযোগিতা করেছেন। ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ, আবদুর রাজ্জাকসহ অপরাপর ছাত্রনেতার সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ ছিল। নিজের গহনা বিক্রি করে ছাত্রলীগের সম্মেলনে টাকা দিয়েছেন। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তি থেকে আয়কৃত টাকায় তিনি অনেক মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন।
বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের দুটি ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণের সঙ্গে বঙ্গমাতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক দায়ের করা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে আমরা সবাই জানি। বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি করে ৩৫ জন বাঙালি নৌ ও সেনাবাহিনীর সদস্য এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র্রদ্রোহের অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হয়। বঙ্গবন্ধু এ মামলায় বিচলিত না হয়ে আইনিভাবে মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আইনজীবীদের অর্থ জোগানোর জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেন। এ মামলায় বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হলে বঙ্গবন্ধুসহ সব রাজবন্দির মুক্তি দাবিতে বাঙালি রাস্তায় নামে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজপথ বিক্ষোভে পরিণত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবকেও গ্রেফতারের হুমকি দেয়। আন্দোলনের বেগবানতায় কার্যত তার সরকার পিছু হটে। পাকিস্তান সরকার এ সময় লাহোরে গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। প্যারোলে মুক্তির সিদ্ধান্তে বেঁকে বসেন ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। তিনি প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে জোরালো আপত্তি জানান। পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি দেখে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবকে প্যারোলে নয়; নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হবে। তিনি কারাগারে শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্যারোলে মুক্তি নিয়ে লাহোর বৈঠকে যেতে নিষেধ করেন। তিনি আরও বুঝতে পেরেছিলেন, শেখ মুজিবের ব্যাপারে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ। পাকিস্তান সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হবে। ফজিলাতুন্নেছার পরামর্শে শেখ মুজিব অনড় থাকেন। প্যারোলে মুক্তির ক্ষেত্রে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে শেখ মুজিবের মুক্তি আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। গণঅভ্যুত্থানের মুখে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মুক্তি লাভ করেন। পরদিন অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বাঙালি তাদের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধি দিয়ে বরণ করে নেয়। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে প্যারোলে মুক্তি না নেওয়ার শেখ ফজিলাতুন্নেছার এই সিদ্ধান্ত যে কোনো মাপকাঠিতে অনন্য হিসেবে স্বীকৃত।
বঙ্গমাতার অপর অনন্যসাধারণ সিদ্ধান্ত হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ। আমরা জেনেছি, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের নেপথ্যে বঙ্গমাতার সঠিক পরামর্শ ছিল। বঙ্গবন্ধুকে সেই সময় তাঁর সহচররা ৭ মার্চের ভাষণের ব্যাপারে নানা পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিচ্ছিলেন। বঙ্গমাতা এ ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুকে যা মন থেকে বলতে ইচ্ছে করে, যা বলা উচিত, তা-ই বলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ‘এবারের সংগ্রাম- আমাদের মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম- স্বাধীনতার সংগ্রাম’ বলে বঙ্গবন্ধুর সেদিনের স্বাধীনতার ডাকে বঙ্গমাতার মনস্তাত্ত্বিক সমর্থন বঙ্গবন্ধুকে সাহস জুগিয়েছিল। বাঙালির স্বাধীনতা ও অধিকারের সংগ্রামে ওপরে বর্ণিত এ দুটি ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহে যদি বঙ্গমাতা প্রত্যক্ষ অবদান না রাখতেন, সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ইতিহাস অন্য রকম হতে পারত।
ঢাকার ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার প্রিয় বাড়িটির কথা আমরা সবাই জানি। এই বাড়িটি নির্মাণের পেছনে বঙ্গমাতার অনেক কষ্ট ও শ্রম আছে। বাসা বদলের ঝক্কি-ঝামেলা এড়ানো এবং স্থিতিশীলতা আনার লক্ষ্যে ৩২ নম্বরে তার বাড়িটি নির্মাণ করা হয়েছিল। আমরা কিছুটা পেছনে ফিরে তাকালে দেখতে পাই, ১৯৫৪ সালে বেগম মুজিব প্রথমবারের মতো ঢাকার গেণ্ডারিয়া এলাকায় বসবাস করতে চলে আসেন এবং ওই এলাকার রজনী চৌধুরী লেনে বাসা নেন। ১৯৫৪ সালে শেখ মুজিব মন্ত্রী হলে বেগম মুজিব গেণ্ডারিয়ার বাসা ছেড়ে ৩ নম্বর মিন্টো রোডের বাড়িতে ওঠেন। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা ভেঙে দিলে ১৪ দিনের নোটিশে ৩ নম্বর মিন্টো রোডের বাসা ছাড়তে বাধ্য হন বেগম মুজিব। এ রকম অনেকবার তাঁর বাসা বদল করতে হয়েছে। অবশেষে ১৯৬১ সালে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কে নিজেদের বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় এবং ওই বছরের ১ অক্টোবর বেগম মুজিব ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে প্রবেশ করেন। আমার প্রিয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার নামে শিক্ষার্থীদের আবাসিক হল আছে। আবাসিক হল আছে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্যকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামেও। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব’ নামে ছাত্রীদের যে আবাসিক হল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে মহীয়সী এই নারীর প্রতি অতি সামান্য সম্মান আমরা জানাতে পেরেছি। বঙ্গমাতার নামে হল নির্মাণ করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবান্বিত। তাঁর প্রতি জাতির কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে শুধু প্রতিষ্ঠানের নাম নয়; তাঁর আদর্শ জাতি তথা নারী জাতিকে অনুপ্রাণিত করতে পারলেই হবে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।
পরিশেষে বলতে পারি, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যত বেশি আলোচনা হবে, বঙ্গমাতার অবদান তত বেশি উদ্ভাসিত হবে। বঙ্গমাতার বিশালত্বের অজানা নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হবে। বাংলার রাজনীতির ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার নাম চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

লেখকঃ বাংলাদেশের প্রথম মহিলা উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সৌজন্যেঃ দৈনিক সমকাল